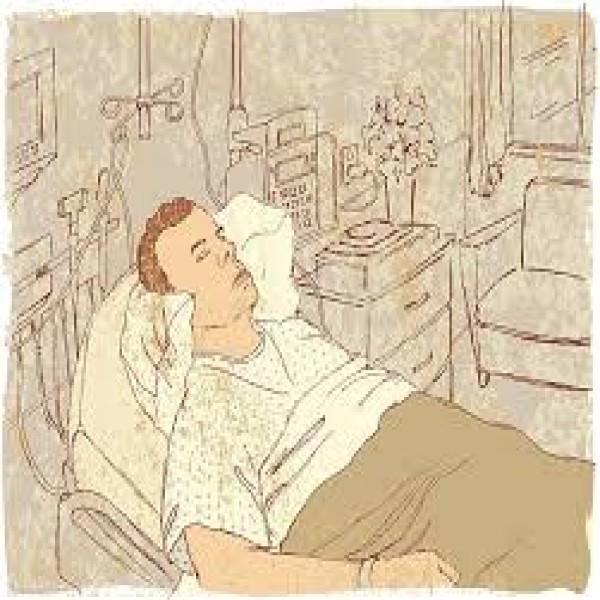
অজ্ঞান রোগীর দশ মুখি যত্ন
ভূমিকা- একজন অজ্ঞান রোগী –এক জন অসহয়ায় মানুষ- তিনি হতে পারেন আপনার প্রিয়জন, নিকটস্থ যে কেউ, আবার একেবারেই অচেনা- পরিচয় যাই হোক না কেন, সেবা করতে গিয়ে নিকট জনেরা প্রায়ই অনেক সমস্যার মুখোমুখী হয়ে থাকেন, মনে সৃষ্টি হয় অনেক জিজ্ঞাসা। কেন এমন হয়? কি ভাবে এই রোগীর যতœ নেওয়া উচিৎ? কোন উপায়ে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব? এর কিছু উত্তর, কিছু সমাধান নিয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস- আশা করছি কিছুটা হলেও আপনাদের উপকারে আসবে। অজ্ঞান রোগীর দশ মুখি যতœ মাথায় আঘাত, স্ট্রোক বা যেকোনো কারনে রোগী অজ্ঞান হোক না কেন-এ সমস্ত রোগীর জন্য নার্সিং কেয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা যেমন নবজাতকের পরিচর্যা করেন, সৃষ্টিকর্তা যেমন সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেন এই রোগীর জন্য সেবা প্রদানকারীর তেমনই মমত্ত্ববোধ ও দ্বায়িত্বজ্ঞান থাকতে হবে। এই তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণভাবে বিষেসজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স এবং সহযোগী ব্যক্তিদের মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে নার্সিং স্টাফদের পাশাপাশি রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা সেবা প্রদানের জন্য সহযোগিতা করেন। আর এর ফলে রোগী বাড়ী যাওয়ার পর রোগীর সেবা শুশ্রষা আত্মীয় স্বজন হাসপাতালের মতই সুন্দর ভাবে করতে পারেন। কারণ রোগী হাসপাতালে থাকাকালীন চিকিৎসা সহযোগী হিসাবে লব্দ অভিজ্ঞতার ফলে নিজেদের গড়ে নিতে পারেন। বর্ননার সুবিধার জন্য সম্পুর্ন বিষয়টিকে নিম্নলিখিত দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- ১. খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা ২. ত্বকের যতœ ৩.প্রসাবের রাস্থার যতœ ৪. পায়খানার রাস্থার যতœ ৫. চোখের যতœ ৬. শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন ৭. মুখগহ্বরের যতœ ৮. শ্বাস নালীর যতœ ৯. শোওয়ানোর নিয়ম ও পোষাকের যতœ ১০. ফিজিওথেরাপী অজ্ঞান রোগীর সেবা দেওয়ার জন্য একটি সুশৃঙখল সেবা প্রদান কারী টিম যেখানে ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, আয়া আর রোগির স্বজনেরা একসঙ্গে কাজ করে থাকেন। ১। খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সহায়তা- অজ্ঞান রোগীকে সাধারণত দুই ভাবে খাওয়ানো যায়- • মুখ ও অন্ননালীর মাধ্যমে খাবার দেওয়া- o স্বাভাবিক ভাবে মুখে খাবার দেওয়া o নাকের নলের মাধ্যমে খাবার দেওয়া o গ্যাস্ট্রোসটোমী নলের মাধ্যমে খাবার সরাসরি পাকস্থলিতে পৌছে দেওয়া। • স্যালাইনের মাধ্যমে শিরায় খাবার পৌঁছে দেওয়া। মুখে স্বাভাবিক খাবার দেওয়ার নির্দেশনা সমূহ - o যেসব রোগীর জ্ঞান আছে বা o খেতে গেলে বিষম খায় না এবং o পর্যাপ্ত খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের নাকে নল দিয়ে খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই, মুখেই খেতে পারে। কোন কোন রোগীকে নাকের নলের মাধ্যমে খাবার দিতে হবে? • অজ্ঞান এবং • খেতে গেলে বিষম খায় • ঢোক গিলতে পারেনা, • খেতে গেলে নাক দিয়ে পানি চলে আসে। এমন রোগীদের নাকের নলে খাবার দেওয়াই ভাল, কখন নাকে নলদেওয়া বিপদজনক?- • স্ক্যাল বেজ ফ্রাকচার (মাথার নীচের ভাঙ্গা), • মুখমন্ডল ও অন্ননালীতে মারাত্মক আঘাত, • খাদ্য নাড়ীর জটিলতা থাকলে এসব ক্ষেত্রে শিরায় স্যালাইনের মাধ্যমে শরীরের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করা হয়। সম্পূর্ন পুষ্টি শিরার মাধ্যমে দেওয়া হলে তাকে টোটাল প্যারেন্ট্রাল নিউট্রিশন বা টি.পি.এন বলা হয়। নাকের নল (রাইলস টিউব) এর মাধ্যমে খাওয়ানোর নিয়ম : ১. খাবার দেওয়ার পূর্বে টিউবের অবস্থান নিশ্চিত করুন - প্রসঙ্গত বলা চলে টিউবের অবস্থান বোঝার জন্য কিছু প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় • টিউবের মাথা একটি পানিপূর্ন কাপের মধ্যে ডুবিয়ে দেখুন বাতাসের বুড়বুড়ি কাটলে বুঝতে হবে টিউব শ্বাস নালীতে চলে এসেছে। • একটি ৫০সিসি সিরিঞ্জে ১০ সি.সি বাতাস পূর্ণ করে দ্রুত টিউবে দিতে হবে, একই সময়ে স্টেথোস্কোপ দিয়ে পেটের উপরের অংশে শব্দ শুনতে হবে, হিসস শব্দ হলে বুঝতে হবে টিউব সঠিক জায়গায় আছে। • টিউবের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক্স-রে করা হয় বা টিউব থেকে বের হওয়া তরলের পি.এইচ পরীক্ষা করা যেতে পারে। ২. গরম বা ঠান্ডা খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনুন। ৩. রোগীর মাথার দিক কমপক্ষে ৪৫০ উচু করুন। বিছানা উচু করা না গেলে রোগীর পেছনের দিকে একজন বসে রোগীর মাথাকে ঘাড়ের উপর নিয়ে নিন। ৪. পঞ্চাস (৫০) সিসি সিরিঞ্জ ফিডিং টিউবের মাথায় ফিট করে রোগীর মাথা থেকে কমপক্ষে একফুট উপরে ধরুন। মাপ মতো খাবার ধীরে ধীরে সিরিঞ্জে ঢালুন। পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া শেষ হলে ২৫সিসি পরিস্কার পানির সঙ্গে প্রয়োজনীয় ঔষধ মিশিয়ে দিন। এবং শেষে ২৫সিসি সামান্য উষ্ণ পরিস্কার পানি দিন, না হলে নল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ৫. এর পর রোগীকে একইভাবে উচু অবস্থায় কমপক্ষে আধাঘন্টা বসিয়ে রাখুন, এই ব্যাপারে ভূলেও জন্য প্রচন্ড সমস্যা হয়ে থাকে। রোগীকে খাওয়ানোর পরে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেওয়া হয় বা অনেক সময় শোয়ানো অবস্থায় খাবার দেওয়া হয়। এ দুটি ঘটনা রোগীকে হাতে ধরে মেরে ফেলার শামিল। তাড়াতাড়ি শোওয়ালে বা শোয়ানো অবস্থায় খাবার দিলে কিছুটা খাবার উপরে উঠে শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে ঢুকে এসপিরেশন নিউমোনিয়া নামক প্রানঘাতি রোগের সুত্রপাত ঘটায়। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ব হই কোনো রোগীকে শোওয়ানো অবস্থায় খাবার দিবনা বা খাওয়ানোর পরে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিবনা। আরও কিছু কথা বলতে হয়- অনেক রোগীর লোক এসে বলে থাকেন- “আমার রোগীতো মুখে খাইব-নলডা খুলে দেন।” এটা মনে রাখবেন এধরনের অনেক রোগীর খেতে গেলে শ্বাস নালীতে খাবার চলে যায়। খাবার শ্বাস নালীতে না অন্ননালীতে ঢুকবে এ রাস্থা ঠিক করার ক্ষেত্রে আলাজিহ্বা ট্রাফিকের মত কাজ করে থাকে। স্ট্রোক,মাথায় আঘাত বা ব্রেইন টিউমারের জন্য অজ্ঞান বা অর্ধজ্ঞান এমনকি সজ্ঞান অনেক রোগীর আলাজিহ্বা সম্পূর্ন প্যারালাইসিস বা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে খাবার কিছুটা খাদ্য নালীতে ঢুকে বাকীটা শ্বাস নালীতে ঢুকে যায়, এই খাবার ফুসফুসে গিয়ে ভয়াবহ এসপিরেশন নিউমোনিয়ার তৈরী হতে পারে। যা কিনা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পাশাপাশি মুখে পর্যাপ্ত খেতে না পারায় রোগী পুষ্টিহীনতায় ভোগেন ও দুর্বল হয়ে যান। সুতরাং নাকের নলে খাবার দেওয়া এইসমস্ত রোগীর জন্য ভাল। ১) টিউবের অবস্থান নিশ্চিত করা হলো ২)পাত্র থেকে অর্ধতরল খাবার সিরিঞ্জে ঢালা হচ্ছে ৩) মোট ২৫০সি.সি খাবার ও ৫০ সিসি পানি সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয় ৩) খাবার দেওয়ার সময় এবং পরে আরও ১৫ মিনিট মাথার দিক বেশ কিছুটা উঁচু করে রাখবেন। চিত্র: রাইলস টিউবে খাবার প্রদান। খাদ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতি হাসপাতালে ডায়েটিশিয়ান ও নিউট্রিশনিস্টের সমন্বয়ে একটি পুষ্টি সহায়তাকারী বিভাগ থাকা আবশ্যক। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় কি খাওয়াবো,কখন খাওয়াবো,কতটা খাওয়াতে হবে ? কী খাওয়াবেন: যে খাবার একটা মানুষ প্রতিদিন স্বাভাবিক ভাবে খেয়ে থাকেন তাই খাওয়াবেন। ভাত, চিড়া, সব্জি, ডিমসেদ্ধ, কাঁটা বিহিন মাছ, হাড় বিহীন মাংস, ফল প্রভৃতি ব্লেন্ডিং করে ১ লিটার খাবার তৈরি করুন। রোগী সুস্থ অবস্থায় ধর্ম সম্মতভাবে যে খাবার খেতে অভ্যস্ত ছিলেন এমন যে কোনও খাবার দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কলা, কাঁঠাল, সজিনা বা বেশি আশযুক্ত খাবার দিলে টিউব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ব্লেন্ডিং এর সময় খাবারের ভেতরে ২৪ ঘন্টায় ২ চামচ খাদ্য লবন ও ১টি স্পিরুলিনা ক্যাপসুল মিশিয়ে নিন। স্পিরুলিনাতে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন ও খনিজ লবন থাকে। এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ আলাদাভাবে তৈরী রাখুন। মিশ্রিত (ব্লেন্ডেড) খাবার ফ্রীজে স্বাভাবিক (নর্মাল) চেম্বারে রাখা উচিৎ। পরিপাকে কষ্ট হয় এমন বেশী ঝাল মশলা যুক্ত খাবার বা বাসী খাবার দেওয়া উচিৎ নয়। দুধ (যে কোন দুধ দেওয়া যায়, গরুর দুধ দেওয়াই ভালো, দুধ না পাওয়া গেলে অথবা সহ্য না হলে প্রীগ্যস্টামিল বা ল্যক্টোজেন নামক পাউডার মিল্ক ব্যবহার করা যেতে পারে), হরলিক্স, সুপ প্রভৃতি মূল্যবান খাবারের পাশাপাশি ডাবের পানি, ভাতের মাড়, ডালের পানিও খাওয়ানো যায়। ব্লেন্ডারের অভাবে হাত পরিস্কার করে ভালভাবে খাবার মেখে ও ছেঁকে নিন। ফ্রিজ না থাকলে এক বারে বেশি খাবার তৈরী করে রাখবেন না। ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার, রক্তে বেশি মাত্রায় চর্বি, কিডনি বা লিভার রোগের রোগীদের জন্য বিশেষ খাবার খাওয়াতে হবে। কখন খাওয়াবেন : সাধারনত সকাল ৬ টা থেকে রাত ১২ পর্যন্ত, ২ ঘন্টা অন্তর মোট ১০ বার খাওয়াতে হবে। বাকী ৬ ঘন্টা রোগীর একটানা ঘুমের জন্য বরাদ্দ থাকে। কতটুকু খাবার দেবেন : রাইলস টিউবের মাধ্যমে বড়দের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর (২০০সিসি অর্ধতরল খাবার + ৫০সিসি পরিস্কার পানি) নলের মাধ্যমে সরাসরি পাকস্থলিতে পৌছে দেওয়া হয়। প্রথম দিনে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক পরিমানে খাবার দেওয়া উচিত এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়াতে হবে। নাকে নল থেকে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? রোগীর জন্য অস্বস্তিকর, আত্মীয় স্বজনের জন্য মানষিক পীড়াদায়ক কিন্তু চিকিৎসার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এই নল থেকে কিছু সমস্যার উদ্ভব হতে পারে- • নল পাকস্থলী থেকে নীচে নেমে বেশি ঢুকে যেতে পারে, আবার উপরে উঠে যেতে পারে, এমনকি বাইরে বেরিয়ে যাওয়া অথবা শ্বাস নালীতে ঢোকার মত ঘটনাও ঘটতে পারে। এজন্য নাকে লাগানো আঠালো টেপ যাতে খুলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিবার খাদ্য প্রদানের পূর্বে নলের অবস্থান পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রয়োজনে নল বের করে আবার নতুন নল দিতে হবে। শোয়ানো অবস্থায় খাবার দিলে অথবা খাবার দেওয়ার পরে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিলে সেই খাবার উপরে উঠে গিয়ে রোগীর শ্বাস নালীতে ঢুকে মারাত্মক প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে একে এসপিরেশন নিউমোনিয়া ( Aspiration Pneumonia) বলা হয়। এ জন্য খাবার দেওয়ার পরে রোগীকে ২০-৩০ মিনিট মাথা উচু করে ধরে রাখুন। শোয়ানোর পূর্বে নাকে এবং মুখে প্রয়োজনে কিছুটা সাকশান দিতে হবে। যদি দীর্ঘ দিন নাকের নলে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে এসপিরেশন প্রতিরোধ করার জন্য পেজ বা পেগ অপারেশনের মাধ্যমে নল সরাসরি পাকস্থলি বা ক্ষুদ্রান্ত্রে বসিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। • টিউবে খাবার দেওয়ার পরে বমি হলে খাওয়ানোর ১৫ মিনিট পূর্বে ডমপেরিডন সিরাপ বা মলদ্বারে ডন এ সাপোসিটরি দেওয়া যেতে পারে। • ডায়রিয়া হতে পারে- এক্ষেত্রে টিউব পরিবর্তন করে দিতে হবে, এবং ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য টিউবে খাওয়ার স্যালাইন দিতে হবে, প্রয়োজনে কলেরা স্যালাইনের ব্যবহার সহ ডায়রিয়ার অন্যান্য চিকিৎসাও করতে হবে। • নিম্নমানের শক্ত নল নাকের ভেতর ইনজুরি করে রক্ত ক্ষরন করতে পারে। সিলিকন টিউবে এই সমস্যা কম হয়ে থাকে। • নল ভাজ হয়ে থাকতে পারে। নাকের নলে খাওয়ানো কখন কিভাবে বন্ধ করবেন ? রোগীর যখন • জ্ঞান ফিরে আসবে, • ঢোক গিলতে পারবে, • নিজের থেকে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন নলের খাবার একটু একটু করে কমিয়ে, ধীরে ধীরে মুখে খাবার বাড়াতে হবে। এভাবে যখন সে সম্পূর্ণ খাবার খেতে পারবে, খেতে গেলে বিষম খাবেনা, তখন নল বাদ দিয়ে মুখে খাবার দিতে হবে। একটি টিউব কতদিন রাখা যায়? সাথারন টিউব ---- দিন রাখা চলে, সিলিকন রাইলস টিউব সব থেকে ভাল - কারন নরম এবং ক্ষতি কম করে, ফলে সিলিকন টিউব---দিন রাখা যায়। টোটাল প্যারেন্ট্রাল নিউট্রিশন পুষ্টি- পৌছে দেয় সরাসরি ধমনীতে শিরায় স্যালাইনের মাধ্যমে পুষ্টি প্রদান বা প্যারেন্ট্রাল নিউট্রিশন- এই পদ্ধতিতে পুষ্টি উপাদান সরাসরি রক্তে পৌছে যায় এবং অত্যন্ত কার্যকরী। কিন্তু এ ব্যবস্থা ব্যয় বহুল এবং অনেক ধরনের জটিলতার ঝুকি থাকায় সচরাচর অনুসরণ করা হয় না। তবে দীর্ঘদিন নাকের নলে খাবার দেওয়া হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে নাকের নলের পাশাপাশি কিছু পুষ্টি শিরায় স্যালাইনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, কারন একটানা শুয়ে থাকা এবং কিছু কারনে খাদ্য নাড়ীর খাবার হজম করার ক্ষমতা কমে যায় যার ফলে পর্যাপ্ত উন্নত খাবার দেওয়ার পরেও শরীরে মারাত্মক পুস্টিহীনতা দেখা যায়। সেজন্য কিছু পুষ্টি পাশপাশি স্যালাইনের মাধ্যমে দেওয়া অপরিহার্য। যেমন ফ্যাট বা চর্বির জন্য ইন্ট্রালাইপোজ ১০% (গ্রীনক্রস), প্রোটিন বা আমিষের জন্য ইনফেসল-৪০ ১০%(মিনারিনি) বা নিউট্রিসল-এস ৫% (গ্রীনক্রস)। ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ফ্রুক্টিন ১০%(বেক্সিমকো) ব্যবহার করা যায়। ভিটামিন, লবন সমুহ ও পানির ভারসাম্যের কথা চিন্তা করে খাবারের পরিমান ও অনুপাত ঠিক করতে হবে। রক্তে এলবুমিন নামক প্রোটিন ঘাটতি দেখা দিলে শরীরে পনি জমে যায়, সেক্ষেত্রে ৫% হিউম্যান এলবুমিন (অক্টাফার্ম) নামক দামি ইন্জেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়। ২) রোগীর ত্বকের যত্ন: নবজাতকের শরীরের ত্বক যেমন অত্যন্ত নরম ও কোমল থাকে, দীর্ঘ দিনের অজ্ঞান রোগীর ত্বক তেমনই নরম ও কোমল হয়ে যায়, ফলে অল্প আঘাতে বা শরীরের চাপে প্রথমে বিবর্ন হয়ে পরে ক্ষত হয়ে যায়। সরাসরি পলিথিনের উপর রোগীকে শোয়াবেন না এবং খেয়াল রাখতে হবে কোনো বিছানা যেন ভিজা না থাকে। শরীরের কোথাও যেন ঘাম-ময়লা জমে না থাকে। মাঝে মধ্যে উষ্ণ পানিতে লিকুইড সোপ গুলে ত্বক স্পঞ্জ করে দিন। তার পরে শরীরে বেবি টেলকম বা বাচ্চাদের গায়ে মাখার পাউডার দিয়ে দিন। প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর পাশ ফেরাতে হবে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শোওয়ানোর জন্য এয়ার মেট্রেস ব্যবহার করা অবশ্যই উচিৎ, এয়ার মেট্রেস ব্যবহার করলে বেডসোর হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। এছাড়া নিউম্যাটিক কুশন ব্যবহার করা উচিৎ, এগুলি দেখতে অনেকটা বাতাস ভর্তি রিং বা ফুলানো টিউবের মতো। ক্ষতস্থান বা ক্ষত হতে পরে এমন যায়গা রিং এর মাঝে রেখে শোয়ালে বিপন্ন জায়গাটি নিরাপদে থাকে। বেডসোর হলে তা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও পীড়াদায়ক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্ষত স্থানে বিভাসিন স্প্রে বা টেগাডার্ম নামক ড্র্রেসিং ব্যবহার করুন অথবা এগ্রোমেড টেরাসিল নামক মলম ব্যবহার করা যেতে পারে। কানের জন্য গ্লাভস দিয়ে কুশনিং ইকরা যায়। ৩) প্রসাবের রাস্থার যত্ন: অজ্ঞান রোগী নিজে থেকে প্রসাব করতে পারেনা এমনকি প্রসাবের কথা বলতেও পারেনা সেক্ষেত্রে ক্যাথেটার দিতে হবে নতুবা প্রসাব থলিতে জমতে জমতে এক সময় বেরিয়ে আসে ঠিকই কিন্তু বাড়তি প্রসাব থলিতে থেকে যায়, যার ফলে কিডনির ক্ষতি হয়, ও জমে থাকা প্রসাবের ভেতরে বারে বারে ইনফেকসন হয়। কখন ক্যাথেটার দিতে হবে? যে সমস্ত রোগী • অজ্ঞান ও নিজে প্রসাব করতে পারেনা • প্রসাবের বেগ নিয়ন্ত্রন করতে পারেনা, • যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য অপারেশন প্রয়োজন • যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য মেনিটোল দেওয়া প্রয়োজন সেই সব ক্ষেত্রে একটি সেলফ রিটেইনিং ফলিস ক্যাথেটার দেওয়া উচিত। যে সব রোগীর প্রসাব হচ্ছে কিন্তু বিছানা নষ্ট হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে পুরুষ রোগীদের জন্য কনডম ক্যাথেটার ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক রোগীর আত্মীয় প্রায়ই বলে থাকেন রোগিতো প্রসাব করছে ক্যাথেটারের প্রয়োজন কি? এক্ষেত্রে একটু বুঝতে ভূল হয় আসলে প্রসাব করতে পারছেনা, প্রসাব জমতে জমতে অনেক চাপ তৈরী হয়ে কিছু প্রসাব বাইরে বেরিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুত্র থলি পরীক্ষা করে দেখবেন কারণ যে অতিরিক্ত প্রসাব থেকে যাচ্ছে কিনা, সেক্ষেত্রে ফলিস ব্যবহার করা অপরিহার্য। ক্যাথেটার থেকে কি জটিলতা তৈরী হতে পারে? • ক্যাথেটার আটকে যাওয়া বা ক্যাথেটার রিটেনশান হতে পারে। ক্যাথেটারে বেলুন ফুলানোর সময় ডিস্টিল ওয়াটার দেওয়া উচিত। নর্মাল স্যালাইন কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ নর্মাল স্যালাইনের ভেতরে থাকা সোডিয়াম ক্লোরাইড লবন বেলুনটি বন্ধ করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে ডিস্টিল ওয়াটার পাওয়া না গেলে সাধারণ পানীয় জল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে লবনাক্ত পানিও একই সমস্যা করে বিধায় উপকূলীয় এলাকায় সাধারণ পানীয় জল কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়। • অজ্ঞান ও অস্থির রোগী খুব নড়াচড়া করে। তখন ক্যাথেটারে টান পড়ে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। একারণে ক্যাথেটার উরু বা থাইয়ের সঙ্গে মাইক্রোপোর নামক সাদা আঠালো কাগজ দিয়ে আটকে রাখা ভাল। প্রয়োজনে এসব রোগীর হাত ধরে বসে থাকতে হবে। না হলে হঠাৎ করে হাত দিয়ে নাকে নল বা ক্যাথেটারে টান ফেলতে পারে। হাতে বক্সার ব্যান্ডেজ করে দেওয়া যেতে পারে। যদি - ক্যথেটার বন্দ্ব হয়ে যায় বা প্রসাবের রাস্থা খুব চিকন থাকে সে ক্ষেত্রে তলপেটে মাঝঝানে একটি সুই দিয়ে প্রসাব বের করে দেওয়া যায়, একে সুপ্রাপিউবিক পাঙ্কচার বলা হয়, তবে দীর্ঘ দিন রাখার প্রয়োজন হলে একই যায়গায় সুপ্রাপিউবিক সিস্টোসটোমি অপারেশন করে টিউব দিতে হয়। ক্যাথেটার খোলার নিয়ম- ক্যথেটার দেওয়া থেকে খোলার পদ্বতি বেশী জটিল ও গুরুত্ত্বপূর্ন। • বেলুনের পানি সম্পুর্ন ভাবে বের করে নিতে হবে না হলে ফোলানো বেলুন টেনে বের করার কারনে প্রসাবের রাস্থা ছিড়ে রক্ত ক্ষরন হতে পারে। • দীর্ঘদিন আছে এমন ক্যথেটার খোলার জন্য জন্য ব্লাডার এক্সারসাইজ বা প্রসাবের থলির ব্যায়াম করাতে হবে। ক্যাথেটার বন্ধ করে ২ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে, এ সময়ে জমে থাকা প্রসাবের চাপের জন্য রোগী যদি প্রসাবের বেগ এসেছে এ কথা বলতে পারে অথবা আকার-ইঙ্গিতে বুঝাতে পারে তবে ক্যাথেটার খুলে দেওয়া যায়, না বলতে পারলে ১ ঘন্টা খোলা রেখে আবারও ব্লক করে দিতে হবে। যতক্ষণ বলতে না পারে ততক্ষণ ২ ঘন্টা বন্ধ ও ১ ঘন্টা খোলা এই কার্যক্রম চলতে থাকবে। ক্যাথেটার কতদিন রাখা যায়? সাধারন ক্যাথেটার---------------দিনের বেশি রাখা উচিৎ নয়, তবে সিলিকন ক্যাথেটার কিছু দিন বেশী রাখা যায়। গুরুত্ব পূর্ন ভূল- অনেকে ইউরো ব্যাগ ফ্লোরে রেখে দেন যার কারনে মুত্রনালীতে টান পড়ে রক্তক্ষরন হতে পারে। খেয়াল করে দেখবেন রোগীর বিছানার পাশে ব্যাগ ঝুলানোর ব্যবস্থা থাকে, অনুগ্রহ করে ব্যাগটিকে জায়গামত ঝুলিয়ে রাখুন। ৪) পায়খানার রাস্থার যত্ন: যারা মুখে স্বাভাবিক খাবার গ্রহণে অক্ষম এবং সবসময় শুয়ে থাকেন তাদের পায়খানা কঠিন হয় এবং পেট ফুলে যায়। নিয়মিত খাবারে শাক সব্জি ব্যবহার করতে হবে। যদি শুকনা শক্ত পায়খানা মলদ্বারে আটকে থাকে সেক্ষেত্রে হাতে গ্লাভস পরে শক্ত পায়খানা বের করে দিতে হবে(ম্যানুয়াল ইভাকুয়েশন)। খাদ্য নাড়ীর গতি ঠিক থাকলে নাকের নলে নিয়মিত অসমোটিক লেক্সেটিভ (লেকটুলোজ) ঔষধ যেমন অসমোল্যাক্স বা মিল্ক অব ম্যগনেশিয়া ব্যবহার করা যায়। এছাড়া নাকের নলে ইছবগুলের ভূষিও ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে রোগীর পরিচর্যাকারী প্রতিবার পায়খানা করার পরে পায়খানার রাস্তার চারপাশ নরম কাপড় দিয়ে পরিস্কার করে দেবেন - যাতে করে মলদ্বারের আশেপাশের কোমল এলাকা বা (পেরিনিয়াম) শুকনা থাকে। পাশাপাশি গ্লিসারিন সাপোসিটরি দিতে হবে। তাতেও কাজ না হলে এনেমা সিমপ্লেক্স বা ফ্লিট এনেমা খুবই কার্যকরী। ৫) চোখের যত্ন: অনেক অজ্ঞান রোগী চোখ খোলা রাখেন এবং চোখের পলক ফেলতে পারেন না। তাদের চোখে মলম বা আই অয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। প্রয়োজনে প্যাড ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে টার্সোরেফি নামক ছোট অপারেশনের মাধ্যমে চোখের দুই পাতা সেলাই করে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়। না হলে চোখ খোলা থাকার কারনে চোখের কর্নিয়ার ক্ষতি হতে পারে। ৬) শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন: শীতের সময় পর্যাপ্ত শীতের কাপড় এবং গরমে হাত পাখার বাতাস বা ফ্যান বা এয়ার কুলার ব্যবহার করতে হবে। ঢিলা পোষাক পরাতে হবে। টাইট ড্রেস, যেমন - বক্ষবন্দনী বা বেল্টের জন্য শ্বাস কস্ট হতে পারে। ৭) মুখগহ্বরের যত্ন: পরিচর্যাকারী নরম ব্রাসে টুথ পেস্ট নিয়ে মুখ পরিষ্কার করে দিন। ছত্রাক প্রতিরোধের জন্য মুখগহ্বরে মাইকোরাল জেল বা এ-মাই জেল ব্যবহার করুন। এপথাস আলসার হলে এপসল পেস্ট ব্যবহার করুন। নকল দাঁত থাকলে খুলে নিন। ৮) শ্বাস নালীর যত্ন: অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে বারে বারে সাকশান দ্বারা মুখ গহ্বর ও শ্বাস নালীর মুখ পরিষ্কার রাখতে হবে। বিষেশ করে খাবার দেওয়ার পরে সাকশন দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। প্রতি রোগীর সাকশান টিউব আলাদা করে রাখুন। সিলিকন সাকার টিউব ব্যবহার করা ভাল। জিহ্বা পিছনের দিকে ঝুলে পড়ে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এক্ষেত্রে এয়ারওয়ে টিউব ব্যবহার করা যায়। ফুসফুসে জমে থাকা কফ বের করার জন্য মাঝে মাঝে পিঠের মধ্যে হালকা থাপ্পড় দিতে হবে। জ্ঞান রোগীকে কাশি দিয়ে কফ তুলে ফেলতে বলতে হবে। ৯) ফিজিওথেরাপি : ফিজিওথেরাপি বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংঙ্গ। সাধারণত ভাবা হয় যে ফিজিওথেরাপি শুধুমাত্র ব্যায়াম, প্রকৃতপক্ষে ফিজিও (শারীরিক) ও থেরাপি (চিকিৎসা) শব্দ দুটি মিলে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ব্যবস্থার সৃষ্টি। একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক অচেতন রোগীর বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল এসেসমেন্টের মাধ্যমে মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিমের সাথে কনস্যাল্ট করে যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে থাকেন যেমনঃ- রোগীর ফুসফুসে কফ জমে গেলে রোগীকে কাত করে পিঠে হালকা থাপ্পড় দেয়া (চেস্ট ফিজিথেরাপী) রোগীকে বিছানায় বিভিন্ন অবস্থান ও উচ্চতায় শোয়ানো ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্রেদিং এক্সারসাইজ দেয়া হয়। রোগীর প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রন না থাকলে বা অনূভূতির সমস্যা থাকলে ব্লাডার এক্সারসাইজ দেয়া হয় যেন মূত্রথলির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, অচেনতন রোগীর প্রতিদিন হাত ও পা’র থেরাপী করানো আবশ্যক যেন রক্ত সঞ্চালন সঠিক/বৃদ্ধি পায় এবং মাংশপেশীতে রক্ত জমাট বাধতে না পারে। কথা বলার জন্যও এক ধরনের ফিজিওথেরাপী আছে, একে স্পিচ থেরাপী বলা হয়। ১০) শোয়ানোর পদ্বতি ও পোষাকের যত্ন:- ‡ivMx‡K নিচের Qwei b¨vq KvZ K‡i w`b, Ge; সাকশান দিয়ে bvK gyL cwi¯‹vi ivLyb| বালিশ কভারে ১,২,৩,৪ প্রিন্ট করা থাকবে। চিত্র: মুখ গহ্বরে সাকশন। রোগীকে পাশ ফিরিয়ে রাখতে হবে, চিৎ করে শোয়ানো মোটেই উচিৎ নয় এবং ২ ঘন্টা অন্তর পাশ পরিবর্তন করতে হবে। পূর্ন বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ১২০০সিসি লালা তৈরী হয়, চিৎ করে শোয়ালে এই লালা বা বমি শ্বাস নালীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে, পাশাপাশি এর কিছু অংশ লালা বা বমি শ্বাসনালীতে গিয়ে এসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে। মাথার দিকটা একটু উচু করে রাখলে ভাল হয়। জামাকাপড় নিয়মিত পরিস্কার করে ইস্ত্রি করে দিতে হবে, দাড়ি শেভ করে দিতে হবে, উপহার হিসাবে ফুল ও চমৎকার ডিজাইনের কার্ড দেওয়া যেতে পারে। টাইট আন্ডার গার্মেন্টস যেমন গেন্জি, জান্গিয়া, বক্ষবন্দ্বনি ব্যবহার না করাই উচিৎ। মহিলা রোগীদের ঋতুচক্রের সময় প্যাড ব্যবহার করতে হবে। প্রতিদিনের পর্যবেক্ষন বা ফলোআপে নীচের বিষয় গুলি বিবেচনা করতে হবে- • রোগীর ওজন (আধুনিক বিছানায় সয়ংক্রিয় ভাবে ওজন মাপার ব্যবস্থা থাকে) • শরীরের কোথাও বির্বনতা বা ক্ষত। • পানি শুন্যতা • ইডিমা বা পানি জমে শরীর ফুলে যাওয়া। • শ্বাস কষ্ট ও ফুসফুসের অবস্থা। • ক্যাথেটার ও প্রসাবের রাস্থার অবস্থা। অজ্ঞান ও জ্ঞানের দশ (১০) দিক আপাত দৃষ্টিতে অজ্ঞান বা আনকনশাসনেচ শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে- এটি অনেকটা পানিতে থাকার মত উপরিস্তরে আধাডোবা থেকে শুরু করে অতল গভীরে তলিয়া যাওয়ার মতই অবস্থা। তাই জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় নিচে লেখা নানা ভাবে প্রকাশ করা যায় : ১. কমা বা গভীর ভাবে অচেতন : কমা এক গভীর অচেতন অবস্থা যেখান থেকে রোগী কোন প্রয়োজনেই জাগ্রত হয় না। অভ্যন্তরীন প্রয়োজন যেমন: প্রসাব/পায়খানার বেগ, ক্ষুধা/তৃষ্ণা, কাম/ক্রোধ আবার বাহ্যিক পরিবর্তন যেমন - শীত/গ্রীষ্ম, তীব্র ব্যাথা, নাম ধরে ডাকা, শব্দ, আলো, কোন কিছুতে সাড়া দেয় না। অর্থাৎ রোগীর মস্তিষ্ক এ পৃথিবীর রূপ/রস/শব্দ/বর্ণ/গন্ধে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনি কাম/ক্রোধ/ভীতি/লোভ প্রভৃতি গুনও আর থাকে না। খুব ব্যাথা দিলে আর্ত চিৎকার বা অর্থহীন (আ-আ, ও-ও, উ-উ, গো-গো) শব্দের মাধ্যমে সাড়া প্রদান করতে পারে। ২. ব্রেইন স্টেম ডেথ : ব্রেইনের স্টেম বা মূল কান্ড (মিডব্রেইন, পনস এবং মেডুলা অবলংগটা) এই অংশ বেচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এখানে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদপিন্ডের চলাচলের উচ্চতর কেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রের কাজ বন্ধ করার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনে ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর ঘনঘটা। এই রোগীর জন্য নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আই.সি.ইউ এ রেখে চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন। যেখানে ভেন্টিলেটর বা কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের মাধ্যমে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। যদি রোগী মোটেই শ্বাস না নেয় তাকে কন্ট্রোল মোডে রাখা হয়- এক্ষেত্রে শ্বাসকার্য পুরাপুরিই মেশিন দিয়ে চলে। আবার কিছু শ্বাস নিলে এস.আই.এম.ভি মোডে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। এস.আই.এম.ভি মোডের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর মেশিন ও রোগী উভয় মিলে শ্বাস কার্যসম্পাদান করে। ৩. ভেজিটেটিভ স্টেট : যেসব অজ্ঞান রোগী নিজে থেকে পায়খানা, প্রসাব, খাওয়া বা অন্য কোনও দৈহিক প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎপিন্ডের গতি স্বাভাবিক ভাবে নিজে থেকে চালাতে পারে তাদেরকে ভেজিটেটিভ স্টেট বলা হয়। রোগী জাগ্রত অথচ অসংবেদনশীল থাকে ফলে ভাল মন্দ বুঝতে পারে না। এমনকি শীত- গরম বা বাইরের কোন উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, একে সেরিব্রাল ডেথ বা নিওকর্টিকাল ডেথও বলা হয়। স্বাভাবিক শ্বাস নেয়, হৃদপিন্ডের গতি স্বাভাবিক থাকে, কারণ ছাড়াই তাকিয়ে থাকে। এসব রোগী কিছুটা বুঝতে পারে আবার অসংবেদনশীল, এই অবস্থা রোগীর স্বজনের জন্য অত্যন্ত মনো বেদনার কারণ হয়ে থাকে। উচ্চ মস্তিষ্ক (সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার) এর অকার্যকারিতায় সংবেদনশীলতা কমে যায় আবার অন্যদিকে ব্রেইন স্টেম কার্যকারী থাকে ফলে হৃদ পিন্ডের চলাচল ও শ্বাসপ্রশ্বাস, চলতে থাকে । ৬-১২ মাস পর্যন্ত এমন অবস্থা চলতে পারে। এদের জন্য প্রয়োজন হয় মা এর মত মমতাময় নার্সিং কেয়ার যাতে করে অনেক রোগীই ভাল হয়ে যায়। ৪. লকড ইন সিনড্রোম: রোগীকে জেলখানায় থাকা বন্দীর সংগে তুলনা করা হয়। সজ্ঞান থাকে, সবই বুঝতে পারে কিন্তু হাত পা নাড়াতে পারে না, কথা বলতে পারে না। চোখ উপরে নীচে উঠাতে পারলেও পাশাপাশি নাড়াতে পারে না। চোখের পাতা নাড়াতে পারেনা এবং চোখ নাড়ানোর মাধ্যমে সাড়া দেয়। পনসের সামনের অংশে আঘাতের জন্য এমন হয়ে থাকে। খুব কমক্ষেত্রে হলেও কিছু রোগী ভাল হতে পারে, তবে পরে হাত পা শক্ত হয়ে যায়। ৫. স্টুপর: বাইরের কোন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, কথা বলতে পারে না। ঝিঁমুনি থাকতে পারে, এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করে যা কোন অর্থ বহন করে না। নিজের উদ্যোগে কোন কাজ করে না। ৬. কনফিউশন: জ্ঞানের আকাশে এক মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা, বোঝে আবার বোঝেও না, ধীর লয়ে চিন্তা করে। প্রায়ই মনে রাখতে পারে না, আবার কিছু কিছু বুঝতে পারে। পাশের লোকজনকে ঠিক মতো চিনতে পারে না। সাধারণত বিপাকে (Metabolism) - সমস্যা, যেমন - কিডনি বা লিভারের অকার্যকারিতা, বা বিভিন্ন ধরনের বিষক্রিয়ার জন্য এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে। ৭. ডেলিরিয়াম: রোগী একদিকে অস্থির উত্তেজিত থাকে আবার অন্যদিকে ধোয়াশাছন্ন চিন্তার ফলে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এ এক উন্মত্ব অবস্থা, ভুল বকা, গালাগালি করা, প্রয়োজন না হলেও পায়খানা প্রসাব করার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। এমনকি অতিমাত্রার সঙ্গমলিস্পাও দেখা দেয়। অশালীন কথা বললেও এসব রোগীদের উপর রাগ করা ঠিক নয়। কারন রোগীতো অসুস্থ হওয়ার ফলেই এমনটি করছে। ৮. লেথার্জি/অবটানডেশন: একটু ঘুম ঘুম ভাব, পূর্ণ সচেতন নয়। কিন্তু ডাক দিয়ে কথা বললে স্বাভাবিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। ৯. সিনকোপ (ফেইন্ট): অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য অজ্ঞান হয়ে আবার খানিক পরে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ অল্প সময়ের জন্য বাধাগ্রস্থ হলেও এমনটি হতে পারে। হৃদপিন্ডের রোগ, ঘাড়ে রক্তসরবরাহে বাধা বা কিছু ঔষধের জন্য সিনকোপ হতে পারে। ১০. ঘুম বা নিদ্রা: গ্রীক মাইথোলজিতে ঘুমের দেবী ‘সোমনা’ আর হিন্দু মাইথোলজীতে ঘুমের দেবী ‘নিদ্রা’। নিদ্রা এক চক্রাকার ছান্দিক শান্তিময় অচেতন অবস্থা যেখান থেকে অভ্যন্তরীন বা বাহ্যিক যে কোন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হওয়া সম্ভব। আসুন কতগুলি প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ জেনে নেই- ১. হেমিপ্লেজিয়া/হেমিপেরেসিস - কোন একদিকের হাত পা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেলে হেমিপ্লেজিয়া আর দুর্বল হলে হেমিপেরেসিস (হেমি অর্থ অর্ধেক, প্লেজিয়া অর্থ সম্পূর্ণ অচল আর পেরেসিস হচ্ছে দুর্বলতা)। প্রায়ই একটি প্রশ্ন শোনা যায় - আক্রান্ত মস্তিষ্কের উল্টা দিকে হেমিপ্লেজিয়া/হেমিপেরেসিস হলো কেন? এটাই সৃষ্টির অপার রহস্য - শরীরের প্রতিটি অংঙ্গের অবস্থান ব্রেইনে ঠিক উল্টা দিকে থাকে। যার ফলে ব্রেনের যেদিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় শরীরে তার উল্টা পাশে দুর্বলতা বা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়। ২. মনোপ্লেজিয়া/মনোপেরেসিস - কোন এক হাত বা পা অচল /দুর্বল হয়ে যাওয়া (মনো অর্থ এক)। ৩. প্যারাপ্লেজিয়া/প্যারাপেরেসিস-দুই পা অচল/দুর্বল (প্যারা অর্থ দুই)। ৪. কোয়াড্রিপ্লেজিয়া/কোয়াড্রিপেরেসিস - চার হাত - পা অচল/দুর্বল । ( কোয়াড্রি অর্থ = চার) ---------০--------
